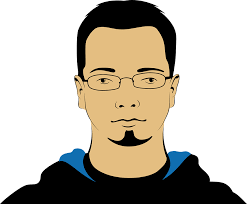


দৃশ্যপট ডেস্ক:
সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া যা সময়ের দাবি নিয়ে কথা বলে। বাংলায় ‘সংস্কার’ কথাটির অর্থ হলো মেরামত করা, সংশোধন করা । সমাজ বা রাষ্ট্র সংস্কার এর অর্থ হল সমাজের বা রাষ্ট্রের দোষ-ত্রুটি দূরীকরণ, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির নবীকরণ। এই অর্থে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতেও সংস্কারের একই ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে। মানব জীবনে সংস্কার কতটা প্রয়োজন তা বোঝা যায় মানব ইতিহাসের আদিম সামাজিক যুগ থেকে আধুনিক সামাজিক যুগের দিকে তাকালে। এই সময়গুলোতে বিস্তর সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। একটি চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । এই আধুনিক যুগে মানুষের জীবন ব্যবস্থায় সমাজ বা রাষ্ট্রকে যত বেশি কল্যাণকামী করতে চাইবেন তত বেশি সংস্কারের প্রয়োজন হবে। সংস্কার নতুন কোন বিষয় নয়। পৃথিবীতে মানব জীবনের শুরু থেকেই মানুষের চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করে বার বার শুধু নয় বহু বার সংস্কার সংঘটিত হয়েছে।
ষোল শতকের পশ্চিমা চার্চে সংঘটিত একটি ধর্মীয় বিপ্লব থেকে সংস্কারের ধারণাটি প্রথম আমাদের সামনে আসে যার নেতৃত্বে ছিলেন মার্টিন লুথার এবং জন ক্যালভিন। সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব থাকার কারণে তখনকার সংস্কার আন্দোলনটি খ্রিস্টধর্মের তিনটি প্রধান শাখার মধ্যে একটি প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হয়ে ওঠে । এটি ছিল ইউরোপে পশ্চিম খ্রিস্টধর্মের একটি প্রধান ধর্মতাত্ত্বিক আন্দোলন যা ক্যাথলিক চার্চের পোপতন্ত্র এবং তাদের কর্তৃত্বের জন্য একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল । রেনেসাঁর শেষের দিকের কথা, যখন এমন একটি সংস্কার আন্দোলন প্রোটেস্ট্যান্টবাদের সূচনা করে এবং ফলস্বরূপ পশ্চিমা খ্রিস্টধর্মের মধ্যে একটি বড় বিভেদ সৃষ্টি করে। দৃশ্যত এখান থেকেই সংস্কার আন্দোলনের যাত্রা শুরু। এই আন্দোলন মানুষের মনে সংস্কার চেতনার বীজ বপন করেছিল এবং পরবর্তীতে তা ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সহ মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসের দীর্ঘ এই সংস্কার যাত্রায় মানুষের প্রয়োজন এবং দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশ এই সংস্কার চেতনার সুফল ভোগ করলেও আমরা বাংলাদেশীরা স্বাধীন দেশ পেয়েও সেই সুফল ভোগ করতে পারিনি। এদেশের সংস্কার চেষ্টা একেবারে থেমে ছিল ব্যাপারটা সেরকম নয়। দেশ স্বাধীনের পর থেকে আজ পর্যন্ত বার বার বিভিন্ন ধরনের খারাপ অভিজ্ঞতা থাকলেও রাষ্ট্র বা রাজনীতিতে বড় কোন সংস্কার সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এর জন্য এদেশের রাজনীতিবিদদের অবজ্ঞা বা অনিচ্ছা বহুলাংশে দায়ী। সংস্কার শব্দটি নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই যথেষ্ট এলার্জি আছে। তারা সংস্থারপন্থীদেরকে আলাদা করে দেখেন এবং যেকোনো রাজনৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদেরকে বয়কট করা হয়। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে সংস্কার রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করতে পারে, সংস্কার রাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। সেক্ষেত্রে গঠনমূলক সমালোচনাকে সহ্য করতে হবে এবং গঠনমূলক সমালোচনার পথকে সহজ করতে হবে। রাজনীতিবিদদের পরমত সহিষ্ণু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে। এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আত্মসমালোচনার অভ্যাস একদমই নাই। সমালোচনাকারীকে সব সময় নেগেটিভ ম্যান হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। দুঃখের বিষয় হলো এদেশে সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক আত্মসমালোচনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্য তার নিজ দলের ভুলত্রুটি নিয়ে কথা বলতে পারে না, সমালোচনা করতে পারে না, প্রতিবাদ করতে পারে না। এক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা আছে। এই নিষেধাজ্ঞা রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে যে কোনো সংস্কার উদ্যোগের সবচাইতে বড় বাধা। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি যেমন ভুলের উর্ধ্বে নয় তেমনি কোন রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্র ভুলে উর্ধ্বে থাকতে পারে না। সেই ভুলগুলো সবার চোখে সমানভাবে ধরা পড়ে না। আর এজন্যই আত্মসমালোচনা ও সমালোচনার সুযোগ উন্মুক্ত থাকা দরকার। এক্ষেত্রে প্রথমে দরকার পড়বে রাজনীতিবিদদের পরিশুদ্ধি। দলকানা আচরণ থেকে রাজনীতিবিদরা বের হতে না পারলে রাজনীতি বা রাষ্ট্র কখনোই পরিশুদ্ধ হবে না। গঠনমূলক সমালোচনা করার জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয় যা অর্জন করতে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত সততা ও স্বচ্ছতা থাকতে হবে। একজন সমালোচকের মধ্যে অবশ্যই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জ্ঞান থাকতে হবে। শুধুমাত্র ভুল ধরা অথবা সমালোচনার উদ্দেশ্য সমালোচনা করলে হবে না, সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করতে হবে। আজ গণ মানুষের মধ্য থেকে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের জোর দাবি উঠেছে। দেশের মানুষ ঘুনে ধরা পুরনো রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে সুস্থ সুন্দর গণতান্ত্রিক চর্চার পরিবেশ চায়। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও এখন সেই চেতনা ফিরে এসেছে। এখন দেশের ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই পঠনমূলক সংস্কারের চিন্তা চেতনা দেখা যাচ্ছে। দলগুলোর নেতারা এখন এসব বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলছেন। বর্তমান সময়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র ভেতরে-বাইরে সংস্কার চেতনা দৃশ্যমান। জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি ভবিষ্যতে ‘জাতীয় সরকারের’ মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করতে চায় বলে জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘স্বাধীনতার পর একটা জাতীয় সরকারের পরিবর্তে আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসায় দেশ প্রথম দিন থেকেই বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে একটা বিরাট অংশ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশ গঠনে কোনো অবদান রাখতে পারেনি। স্বাধীনতার পরপর জাতীয় ঐক্যের শক্তিকে ব্যবহার না করে সেদিন যে সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে, আগামী দিনে আমরা তার পুনরাবৃত্তি চাই না।’ তারেক রহমান আরও বলেন, ‘এ দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র আর ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা আগামী দিনে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন। যাতে দেশ তাঁদের অবদানের সুফল থেকে বঞ্চিত না হয়।’ জনাব তারেক রহমানের এমন দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান সময়ের সংস্কার চেতনাকে দারুনভাবে উৎসাহিত করেছে। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি’র এমন চিন্তা-চেতনা আমাদের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে সবাই বিশ্বাস করে।
আওয়ামী লীগের অবর্তমানে বিএনপির পরে এই দেশে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতকে বিবেচনা করা যেতে পারে। সেই জামাতের আমীর ডাক্তার শফিকুর রহমানের দেয়া সাম্প্রতিক বক্তব্যগুলো ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। তার দেয়া বক্তব্যগুলো দল মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তার বক্তব্যগুলোতে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে গঠনমূলক রাজনৈতিক সংস্কার এবং টেকসই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মতো অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ডাক্তার শফিকুর রহমান তার দলকে একটি উদার ইসলামী দল হিসেবে মানুষের মধ্যে তুলে ধরতে দারুনভাবে সক্ষম হয়েছেন। তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের উদার চিন্তা-চেতনা ও গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেশব্যাপী জনসাধারণের নিকট স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিতে সফল হয়েছে। এই কারণে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির হার বিবেচনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এখন সবার উপরে। বিগত প্রায় ১৭ বছরের অধিক সময় ধরে ফখরুদ্দিন-হাসিনা সরকারের ভয়াবহ জুলুম-নির্যাতনের পর দলটি কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে এবং তাদের নেতা-কর্মীর সংখ্যা কমেছে নাকি বেড়েছে তা নিয়ে জনমনের একগাদা প্রশ্নের আশাতীত উত্তর দিতে তারা এক মুহূর্তও সময় নেয়নি। জামায়াত দারুন ভাবে ফিরে এসেছে এবং হাসিনা পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন ইউনুস সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। হাসিনা পরবর্তী রাজনৈতিক সহিংসতায় জামায়াতে ইসলামীর সম্পৃক্ততা ছিল না বললেই চলে। বিশেষ করে দলটির কেন্দ্রীয় আমীরের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা মানুষের ধারণা একদম বদলে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ জামায়াতের নিকট থেকে যে প্রতিঘাত আশা করেছিল বাস্তব চিত্র ছিল তার সম্পূর্ণ উল্টো। জামায়াতের এই বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থান দেশের রাজনৈতিক সংস্কারকে দারুন ভাবে প্রভাবিত করবে। একই সাথে এদেশের অন্যান্য ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করছে।
আমি একজন সাধারন নাগরিক এবং গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে যা দেখেছি তা কোনো পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের সাথে তো যায়ই না বরং ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের সাথেও যায় না। আমার ছোট্ট জীবনের সেই অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। যেখান থেকে সংযোজন ও বিযোজনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে গঠনমূলক সংস্কার সাধন করা সম্ভব।
প্রথমত, সাংবিধানিক সংস্কার:
সংস্কারের কথা যখন আসবে তখন প্রথমেই আসবে নতুন বাংলাদেশের নতুন সংবিধানের কথা। এ দেশের বর্তমান সংবিধান নিয়ে বিস্তর সমালোচনা আছে। একটা সংবিধান জাতীয় শাসনব্যবস্থার একমাত্র দিকনির্দেশক। কিন্তু একে যাচ্ছেতাইভাবে গত ৫৩ বছরে কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। যে শাসন করবে, সেই শাসিত হয়েছে। এর কারণ হলো, এই সংবিধানের অস্পষ্টতা ও পরস্পর সাংঘর্ষিক (ধারা-উপধারা) অনুচ্ছেদগুলো। কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়ে সহজ কথায় যে পরামর্শগুলো দিতে চাই তা হলো-
এক. ভবিষ্যতের সংবিধানটা এমন ভাবে লিখতে হবে যেন আকারে ছোট হয় এবং একজন নাগরিক পড়া মাত্রই তা বুঝতে পারে। সাধু ভাষার মারপ্যাঁচে মূল কথাটা যেন দুর্বোধ্য হয়ে না ওঠে।
দুই. নতুন সংবিধানে বিচার বিভাগকে প্রথমে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখতে হবে। এরপর আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী বিভাগগুলোকে রাখতে হবে। বিচার বিভাগের প্রাধান্যতা বাকি দুটি বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে।
তিন. সংবিধানে দ্বৈত নাগরিকত্ব বিধান থাকতে পারে শুধুমাত্র অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কেউ যদি ভিনদেশের নাগরিকত্ব নিতে ইচ্ছুক থাকে, তবে তাকে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে এবং রাজনীতি থেকে অবসর নিতে হবে। তাহলে এই দেশে বিদেশি পাসপোর্টধারী ব্যক্তিদের রাজনীতি ব্যবসা বন্ধ হবে।
চার. সংবিধানে বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে কিছু থাকবে না। আইনকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।
পাঁচ. বর্তমান সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জনস্বার্থে যেকোন কথা বলতে পারবে। এক্ষেত্রে নিজ দল বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।
ছয়. বাংলাদেশের নতুন সংবিধান গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে। কোনো সরকার শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে না। যেকোনো ধরনের পরিবর্তন বা সংশোধন কেবল মাত্র গণভোটের মাধ্যমে হতে হবে। গণভোট ছাড়া কোনো সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ইচ্ছে মতো সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদে বিল আনতে পারবে না।
দ্বিতীয়ত, সরকার ব্যবস্থায় সংস্কার:
বাংলাদেশের চলমান সরকার ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো হতে পারে-
এক. নতুন বাংলাদেশের ভবিষ্যতের সরকার ব্যবস্থা হবে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র।
দুই. নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ক্যাবিনেট দ্বারা গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রচলিত সংসদীয় প্রথাতেই নিযুক্ত হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমুল পরিবর্তন আনতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে নয় বরং জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।
তিন. বর্তমান সরকার ব্যবস্থায় একজন প্রধানমন্ত্রীর হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করা আছে তা এক সময়ের বহুল আলোচিত রাশিয়ান জার সম্রাটদের হাতেও ছিল না। এখানে ক্ষমতার লোড শেয়ারিং এর প্রয়োজন আছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবি। এককভাবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে কুক্ষিগত করা ক্ষমতাগুলোর মধ্যে অরাজনৈতিক ধরনের ক্ষমতা যেমন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন-বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদিতে রাষ্ট্রপতিকে সম্পৃক্ত করে তার কর্মপরিধি বা কার্যকর কর্ম তৎপরতা বাড়ানো দরকার।
চার. রাষ্ট্রপতি কোনো দলীয় প্রার্থী হবেন না। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য সমর্থন পাবেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন পাচ বছরের জন্য। একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে এক মেয়াদের বেশি থাকতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতির বক্তব্য কি হবে তা শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী বা তার মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে না।
তৃতীয়ত, বিচার বিভাগীয় সংস্কার:
বিচার বিভাগের সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত করে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। হাইকোর্ট বিভাগের কার্যক্রম শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের প্রত্যেকটা বিভাগীয় শহরে হাইকোর্ট বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে করে ন্যায়বিচার প্রার্থীদের বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ হয়।
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন এবং অ্যাপিলেট ডিভিশনের বিচারপতি নিয়োগের সময় খতিয়ে দেখতে হবে যে, আগ্রহী প্রার্থীর কোন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা। কোন অ্যাডভোকেট তার জীবনের কোন এক সময় কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এমন ব্যক্তিকে বিচারপতি নিয়োগের জন্য মনোনীত করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত অরাজনৈতিক সিনিয়র এ্যাডভোকেটদের নিয়ে একটা প্যানেল তৈরি করতে হবে এবং তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তদন্ত করতে হবে। এই তদন্তে তিনটা বিষয় খুবই গুরুত্ব দিতে হবে-
এক. কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে সে কখনো সম্পৃক্ত ছিল কিনা।
দুই. কোন রাজনৈতিক দল বা দলের অঙ্গ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা।
তিন. ব্যক্তি জীবনে তিনি কতটা সৎ এবং নীতিবান।
সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত সকল পর্যায়ে নিম্ন আদালতের বিচারক (সহকারী জজ) নিয়োগের চলমান প্রক্রিয়া বহাল থাকতে পারে। তবে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি)’কে অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে।
চতুর্থত, রাজনৈতিক দলে সংস্কার:
সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার সবচাইতে বেশি জরুরি। প্রস্তাবিত সকল ধরনের সংস্কার উদ্যোগ সফল হবে কি হবে না তা অনেকটাই নির্ভর করে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংস্কার উদ্যোগের সফলতার উপর। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সব সময় গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চিল্লাচিল্লি করে কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের দলের মধ্যেই গণতন্ত্রের চর্চা সঠিকভাবে করে না।পরিবারতন্ত্র এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে সবচাইতে বড় বাঁধা। পরিবারতন্ত্র এদেশের বৃহৎ কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে যে, সংশ্লিষ্ট ঐ পরিবারের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে দলগুলোকে সব সময় গণতান্ত্রিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। পরিবারতন্ত্রের সবচাইতে খারাপ দিক হলো ক্ষমতাসীন দল ও রাষ্ট্রের সব কিছুই একটি পরিবারের নিকট জিম্মি থাকে। একথা বললে অবশ্যই ভুল হবে না যে, পরিবারতন্ত্র হচ্ছে আধুনিক রাজতন্ত্র।
এই অবস্থায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে সংস্কারগুলো অবশ্যই করতে হবে তা হচ্ছে-
এক. রাজনৈতিক দলগুলোতে কেউই সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক অথবা সমমানের পদে দুইবারের অধিক থাকতে পারবে না।
দুই. দলীয় প্রধান সরকার প্রধানের দায়িত্ব নিতে পারবেন না অথবা সরকার প্রধান দলীয় প্রধানের দায়িত্বে থাকতে পারবেন না।
তিন. শিক্ষাগত যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সরকারের যেকোনো পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বাছাই এর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে ।
চার. নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীন বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পদের নির্বাচনের সময় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে আবেদনের মাধ্যমে কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। দলীয় নির্বাচনেও ভোট গ্রহন থেকে থেকে শুরু করে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ড নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিগণ পরিচালনা করিবেন। এই ধরণের আনুষ্ঠানিক নির্বাচন ছাড়া কোনভাবেই একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা যাবে না।
রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শর্ত হিসেবে উল্লেখিত বিষয়গুলো অবশ্যই মানার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা যত মজবুত হবে জাতীয় রাজনীতিতে তার প্রভাব ততই ইতিবাচক হবে। বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে চলমান হ-য-র-ল-ব অবস্থা শুধুমাত্র এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মকেন্দ্রিক ও পরিবারতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার কুফল। দলের ভেতর গ্রুপিং তৈরি করা এবং আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজ দলের ভেতর মারামারি করা খুব সাধারন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিতে হবে। একটি রাজনৈতিক দল গঠন থেকে শুরু করে দল পরিচালনায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্দেশিত কিছু গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতি অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। এমন অনেক রাজনৈতিক দল আছে যারা পরিবারতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ম নীতির মধ্যে থেকেও নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক মনে করে। শুধু বাংলাদেশ নয় বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে বেশিরভাগ দেশেই সুশাসন ও গণতন্ত্র উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করেছে। বৈশ্বিকভাবে গণতন্ত্রের পশ্চাৎ যাত্রার একটি দিক হচ্ছে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের লেবাসধারী স্বৈরাচারী শক্তিগুলো নিজেদের কেবল গণতান্ত্রিক বলেই দাবি করে তা নয়, তাদের বক্তব্য হচ্ছে গণতন্ত্রের যেহেতু সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নেই, সেহেতু তাদের চালু করা ব্যবস্থাই হচ্ছে গণতন্ত্র। এর একটি অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত গণতন্ত্র সম্মেলনের সময় গণতন্ত্র নিয়ে চীন সরকারের প্রকাশিত একটি শ্বেতপত্র ‘চায়না: ডেমোক্রেসি দ্যাট ওয়ার্কস’ শিরোনামের দীর্ঘ একটি লেখায় চীন নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে চীন একটি অসাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কেবল চীনই তা করে, তা নয়। অন্যান্য দেশের অগণতান্ত্রিক শাসকেরাও নিজস্ব ভঙ্গিতে তাঁদের শাসনকেই ‘মানুষের কাঙ্ক্ষিত’ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে জাহির করার চেষ্টা করেন। বিগত সময় গুলোতে বাংলাদেশ তাদেরকে খুব ভালোভাবে অনুসরণ করেছে।
স্বৈরতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র ছুড়ে ফেলে গণতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরার আগে আমাদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কার আনতে হবে। সারা বিশ্বে রিপাবলিক গঠনের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তারা গণতন্ত্রের ধারণা কীভাবে বিকশিত হয়েছে সেই বিষয়ে অবগত, তাঁরা এটাও জানেন যে গণতন্ত্রের চারটি মৌলিক আদর্শ রয়েছে; সেগুলো হচ্ছে-
১. জনগণের সার্বভৌমত্ব,
২. প্রতিনিধিত্ব,
৩. দায়বদ্ধতা ও
৪. মত প্রকাশের স্বাধীনতা।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গত দেড় দশকে গণতন্ত্রের যে পশ্চাদপসরণ হয়েছে, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির উত্থান ঘটেছে, রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে গণতন্ত্রের মর্মবাণী এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে তার টেকসই পুনর্গঠনে সুস্থ ধারার গণতান্ত্রিক চর্চাই একমাত্র সমাধান যা সুসম্পন্ন হতে হবে রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে।
সর্বপরি কথা হল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী পার হয়েছে যখন কাঙ্খিত অনাকাঙ্খিত অনেক ঘটনাই ঘটেছে। এই সময়ে স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন একনায়ক হয়েছে, বহুদলীয় গণতন্ত্রের সংসদীয় পদ্ধতির সংবিধান বারবার বলাৎকারের শিকার হয়েছে, পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বেচ্ছাচারিতা রাজনৈতিক দল ও সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে জিম্মি করে রেখেছে। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের বৈষম্যবিরোধী স্লোগান এসব অনিয়ম ও কলুষতাপূর্ণ সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এই অবস্থায় সংস্কারের দাবি যখন জোরদার তখন অনেকেই অনেক রকম সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরছেন। অনেক রকম সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে আমার প্রস্তাবিত সংবিধান, বিচার, নির্বাহী, আইন প্রণয়ন, নির্বাচন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত সংস্কারগুলো মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটা সুন্দরতম রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এ সংস্কারগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে একটা সর্বজনীন জবাবদিহিমূলক জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।
মোঃ ওমর ফারুক খান জুবায়ের
সাংবাদিক ও লেখক।